গৌতম রায়
সরকার প্রাক-প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাক্রম ও মূল্যায়নসহ শিক্ষাব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিকল্পনা আনছে। ২০২১ সাল থেকে শুরু হয়ে এই পরিবর্তন সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হবে ২০২৫ সালে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)-সহ সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো এ কার্যক্রম অনেকটাই এগিয়ে নিয়েছে। গণমাধ্যমে প্রায়ই এ-বিষয়ে খবর প্রকাশিত হচ্ছে। পাশাপাশি, শিক্ষা নিয়ে যারা ভাবনাচিন্তা করেন, তাদেরও অনেকে এসব বিষয় নিয়ে লিখছেন। উল্লেখ্য, এসব লেখার বড় অংশ জুড়ে রয়েছে নতুন পরিবর্তন নিয়ে উদ্বেগ ও শঙ্কা।
এই উদ্বেগ ও শঙ্কার অন্যতম কারণ হিসেবে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট তথ্য না থাকাকে চিহ্নিত করা যায়। অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি, বাংলাদেশের শিক্ষার বেশ কিছু বড় পরিবর্তন শেষ পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষতিই করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা (পিইসিই) বা জুনিয়র সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষার মতো বড় আয়োজনগুলো শিক্ষার্থীকে শিক্ষা-অভিমুখী না করে পরীক্ষা-অভিমুখী করেছে বা প্রকারান্তরে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার্থী হিসেবে গড়ে তুলছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ পরিণত হয়েছে পরীক্ষা-প্রস্তুতির কেন্দ্রে। এসব পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পাওয়ার যে প্রাবল্য দেখা গেছে বিগত বছরগুলোতে এবং জিপিএ ৫-এর ভিত্তিতে বেড়ে ওঠা শিক্ষার্থীদের গুণগত মানের যে-প্রতিফলন পরবর্তী পর্যায়ে দেখা গেছে, তাতে শিক্ষার মান নিয়ে আশাবাদী হওয়ার সুযোগ কম। যদিও জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন কমিটির অন্যতম সদস্য অধ্যাপক ড. জাফর ইকবাল বিভিন্ন সময় বলেছেন, তাঁরা যে খসড়া প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন ২০০৯ সালে, সেখানে এ-ধরনের পরীক্ষার প্রস্তাব করা হয়নি। কীভাবে এই দুটো পরীক্ষা শিক্ষানীতিতে এলো সে-সম্পর্কে তিনি নিজেও অবগত নন। এই দুটো পাবলিক পরীক্ষা নিয়ে অভিভাবকদের ক্ষোভও ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে।
এই উদাহরণ থেকে পরিষ্কার যে, শিক্ষার পরিবর্তন একটি জটিল বিষয় এবং এতে বিশেষজ্ঞের মত ও জনমানুষের চাহিদা উভয়ের প্রতিফলন থাকতে হয়। বিশেষজ্ঞরা যেসব সুপারিশ করবেন, সেগুলো বাস্তবায়িত হলেই যে সবসময় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে— এমনটি না-ও হতে পারে; কিন্তু বিশেষজ্ঞদের যেকোনো চিন্তার পেছনে নির্দিষ্ট যুক্তি ও তথ্য থাকে। বর্তমান পরিবর্তন নিয়ে গণমাধ্যমে যেসব খবর ও মতামত আসছে, সেগুলোর ভিত্তিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে অনেকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন— সেগুলোর অধিকাংশই নেতিবাচক। যারা সেখানে মত দিচ্ছেন, তাদের একটি বড় অংশ যদিও বিশেষজ্ঞ নন, কিন্তু জনমানুষের চাহিদার প্রতিফলন অতীতে কম ঘটেছে বলে সাম্প্রতিক পরিবর্তন তাদের অনেককে শঙ্কিত করছে।
প্রশ্ন হতে পারে, নীতিসম্পর্কিত সমস্ত পরিবর্তনেই কি তাহলে জনমানুষের সম্পৃক্ততা রাখতে হবে? বিষয়টি সেভাবে না দেখে বরং এভাবে বলা ভালো— বড় কোনো পরিবর্তনে জনমানুষ কিংবা অংশীদারবৃন্দকে (stakeholders) শুরু থেকে সম্পৃক্ত রাখা ভালো। এতে সংশ্লিষ্ট কাজে মানুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়, আস্থা বাড়ে, কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহজতর হয় এবং নেতিবাচক অনেক প্রভাব এড়ানো যায়। দুটো উদাহরণ এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হবে।
প্রথমত, কোনো শিক্ষা কমিশন বা শিক্ষা কমিটি যখন কাজ করে, তখন নানা বিষয় নিয়ে কমিটির সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে মতবিনিময় করে। কাজটি দুটো উদ্দেশ্যে করা হয়। একটি হচ্ছে, প্রত্যেক গোষ্ঠীর চাহিদা অনুধাবন করা, এবং অপরটি হচ্ছে, কী সুপারিশ করা হলো সেটি শেয়ার করা। স্বাধীনতার পর এ-দেশে যতগুলো পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে, তার সবগুলোই এভাবে কাজ করেছে। সেখানে বিভিন্ন সেক্টরের বিশেষজ্ঞরা যুক্ত হয়ে পূর্ণাঙ্গ সুপারিশ প্রদান করেছেন। ১৯৭২ সালে গঠিত ড. কুদরাত-এ-খুদাকে চেয়ারম্যান করে গঠিত বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন দেখলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে।
দ্বিতীয়ত, ২০১৩ সালের ৫ অগাস্ট বাংলাদেশে শিক্ষা আইনের একটি খসড়া জনমত যাচাইয়ের জন্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। আইনের নানা বিষয় নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষ এতে মত দেন, বিশেষত বিভিন্ন পেশাগোষ্ঠীর মানুষ একে নেতিবাচকভাবে নেন। একটি বড় ফিডব্যাক ছিলো এই— যদিও এটিকে ‘শিক্ষা আইন’ বলা হচ্ছে, কিন্তু আইনের পরিভাষায় এতে অনেক আইনি বিষয় অনুপস্থিত; বরং একে নীতিমালার মতো করে তৈরি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২০১৬ সালে শিক্ষা আইনের খসড়া পুনরায় মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেয়ার পর মূলত কোচিং ও গাইড বই ব্যবসায়ীরা এর বিপক্ষে নামে। এখন পর্যন্ত নানা জটিলতায় আইনটি আলোর মুখ দেখেনি।
জনমানুষকে নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত করা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ, এতে কাদের স্বার্থ রক্ষিত হবে এবং কীভাবে সেটি বাস্তবায়িত হবে, সেসব বিষয়ে তাই গভীর ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে প্রতিটি ক্ষেত্রেই। বর্তমানে যে পরিবর্তন আনা হচ্ছে, এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন এনসিটিবির বিশেষজ্ঞগণ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষকবৃন্দ। পাশাপাশি, কারিগরি সহায়তা দিচ্ছেন আরও বেশ কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফল ও বিজ্ঞ এবং তাদের আন্তরিক কর্মকাণ্ডে পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় ভালো শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক পাবো বলে আস্থা রাখতে চাই।
বিজ্ঞাপন
কিন্তু, এই আস্থাটি গভীর আস্থা, বিশ্বাস ও প্রত্যয়ে পরিণত হতো, যদি তারা বর্তমান পরিকল্পনা খসড়া করে মতামতের জন্য বিস্তৃত পরিসরে, অন্ততপক্ষে, সংশ্লিষ্ট পেশাজীবিদের মতামত গ্রহণ করতেন। সংবাদপত্রের ভাষ্য অনুসারে, ইতোমধ্যে কিছু বিষয় চূড়ান্ত হয়েছে, কিছু কিছু বিষয়ে কাজ চলছে। যেসব বিষয় চূড়ান্ত হয়েছে, সেগুলো চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বে বড় পরিসরে শেয়ার করা হলে জাতি আরও বেশি উপকৃত হতো বলে মনে করি।
হতে পারে, ইতোমধ্যেই দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ এই কাজটি করেছেন যা আমার জানা নেই। ফলে, যারা এসব বিষয় সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন, এসব বিষয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেন, তাদের অনেকের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, আমার মতোই বিষয়টি নিয়ে তাদের প্রায় সবাই অন্ধকারে রয়েছেন এবং তারাও একইভাবে উদ্বিগ্ন। কিছুকাল পূর্বেও শিক্ষা বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রির ব্যবস্থা ছিলো না বাংলাদেশে। বর্তমানে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, নোয়াখালী, জগন্নাথসহ বেশ কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বিষয়ে বিশেষায়িত ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে। সেখানকার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এসব বিষয় শেয়ার করলে পুরো কার্যক্রমই উপকৃত হতো। পাশাপাশি, বর্তমান পরিবর্তনে আস্থা ও যথার্থতা উভয়ই বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়তো বলে মনে করি। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা নিয়ে কাজ করছেন, এমন মানুষের সংখ্যাও কম নয়। তাদেরকেও যুক্ত করা গেলে আক্ষরিক অর্থেই নতুন এই পরিবর্তন সবার কাছে প্রশ্ন ছাড়াই গ্রহণযোগ্যতা পেতো। মতবিনিময়ের মাধ্যমে তাদের সহায়তা চাইলে তারা বরং সরকারকে আগ্রহসহকারে আন্তরিকতা নিয়ে সহায়তা করতেন বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। অবশ্য, কর্তৃপক্ষ চাইলে এখনও সেই কাজটি করতে পারেন, সেজন্য সময়ও রয়েছে যথেষ্ট।
বতর্মান পরিবর্তনের এই কার্যক্রমের সঙ্গে যারা যুক্ত, তারাও তো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বা প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি রয়েছে কিংবা এই সেক্টরে শিক্ষকতা করছেন বা দীর্ঘদিন কাজ করছেন, তাহলে সমস্যা কোথায়— এমন প্রশ্নও মনে হতে পারে অনেকের। উত্তর হচ্ছে, কোনো সমস্যা নেই, বরং তারা যোগ্য ও দক্ষ বলেই এমন একটি বড় কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু, প্রতি-প্রশ্ন হতে পারে— প্রতিটি ক্ষেত্রেই যেখানে আরও বেশি পেশাজীবি ও বিশেষজ্ঞদের যুক্ত করার সুযোগ রয়েছে কিংবা তাদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে চুলচেরা বিশ্লেষণ দ্বারা উক্ত কার্যক্রমে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ রয়েছে, সেখানে সুযোগটি নেয়া সমীচীন নয় কি? এমনও তো নয় যে, পুরো পরিকল্পনাটি এনসিটিবি বা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে এবং মানুষজনের মত চাওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে অনেকে তাদের মত জানাতে পারতেন। অধিক মানুষের মত সংগ্রহের প্রক্রিয়ায় কোনো লাভ না হলেও ক্ষতি তো নেই!
কাজটির বড় অংশ, বলা যায়, মূল অংশ বাস্তবায়ন করছে এনসিটিবি। প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইটে বর্তমান কার্যক্রমের বিস্তারিত দেয়া নেই, কেবল কিছু কমিটির নোটিশ দেয়া আছে। ‘শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন কোর কমিটি (CDRCC)’ এবং ‘শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়নের ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন’ কমিটিতে যাদের নাম রয়েছে, তাদের সবাই এনসিটিবির সদস্য ও কর্মকর্তা। ধারণা করছি, তারা গোটা কার্যক্রম সমন্বয় করছেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন সেক্টরের বিশেষজ্ঞবৃন্দ সহায়তা করছেন। এর বাইরে ২০১৯ সালের ২৭-৩০ এপ্রিল এনসিটিবির বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষজ্ঞগণ এবং বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের সহায়তায় জাতীয় শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা, শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের বাস্তব অবস্থা যাচাই ও চাহিদা নিরূপণ সমীক্ষার তথ্য সংগ্রহের জন্য নয়টি জেলায় গিয়েছিলেন। তার মানে, অংশীজনদের চাহিদা জানা, তাদের পরামর্শ শোনা বা বক্তব্য শেয়ার করার গুরুত্ব সম্পর্কে এনসিটিবি ওয়াকিবহাল। সেক্ষেত্রে পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার সময় তারা একই কাজ কেন করেনি, তা বোধগম্য নয়।
শিক্ষাব্যবস্থার যেকোনো পরিবর্তনে এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়ে প্রতিটি মানুষের ওপর। বাস্তবতা, উপযোগিতা ও সঙ্গতি বিবেচনায় যেহেতু বড় অংশের মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব নয় বা তাদের মত নেয়া সম্ভব নয়, তাই তাদের প্রতিনিধিত্ব করে এমন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গকে যেকোনো বিষয় চূড়ান্ত করার পূর্বে যুক্ত করা প্রয়োজন। অন্ততপক্ষে, প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই), উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এইচএসটিটিআই), টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (টিটিসি), বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইআর) বা ফ্যাকাল্টি অব এডুকেশন এবং শিক্ষাচিন্তকদের সঙ্গে বর্তমান পরিকল্পনার নানা দিক নিয়ে ভাবনা বিনিময় করা জরুরি বলে আমি মনে করি। এতে যে ব্যয় হবে, সেটি নগণ্য বললেও কম হবে; কিন্তু এ থেকে যে প্রতিদান আসবে, তাকে অমূল্য বলা যায়।
প্রত্যাশিত শিক্ষাক্রম, বাস্তবায়িত শিক্ষাক্রম এবং অর্জিত শিক্ষাক্রমের মধ্যকার দূরত্ব কমাতে হলে এই পরিকল্পনায় শিক্ষাবিশেষজ্ঞ, শিক্ষক-প্রশিক্ষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করা জরুরি। একুশ শতকের জন্য কর্মদক্ষ জনশক্তি এবং দেশ ও সমাজের জন্য দায়িত্বশীল সুনাগরিক তৈরি করতে হলে গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে নিয়মতাত্ত্বিক পদ্ধতি অনুসরণ করেই শিক্ষাক্রম তৈরি করা উচিত।
গৌতম রায়: সহকারী অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়


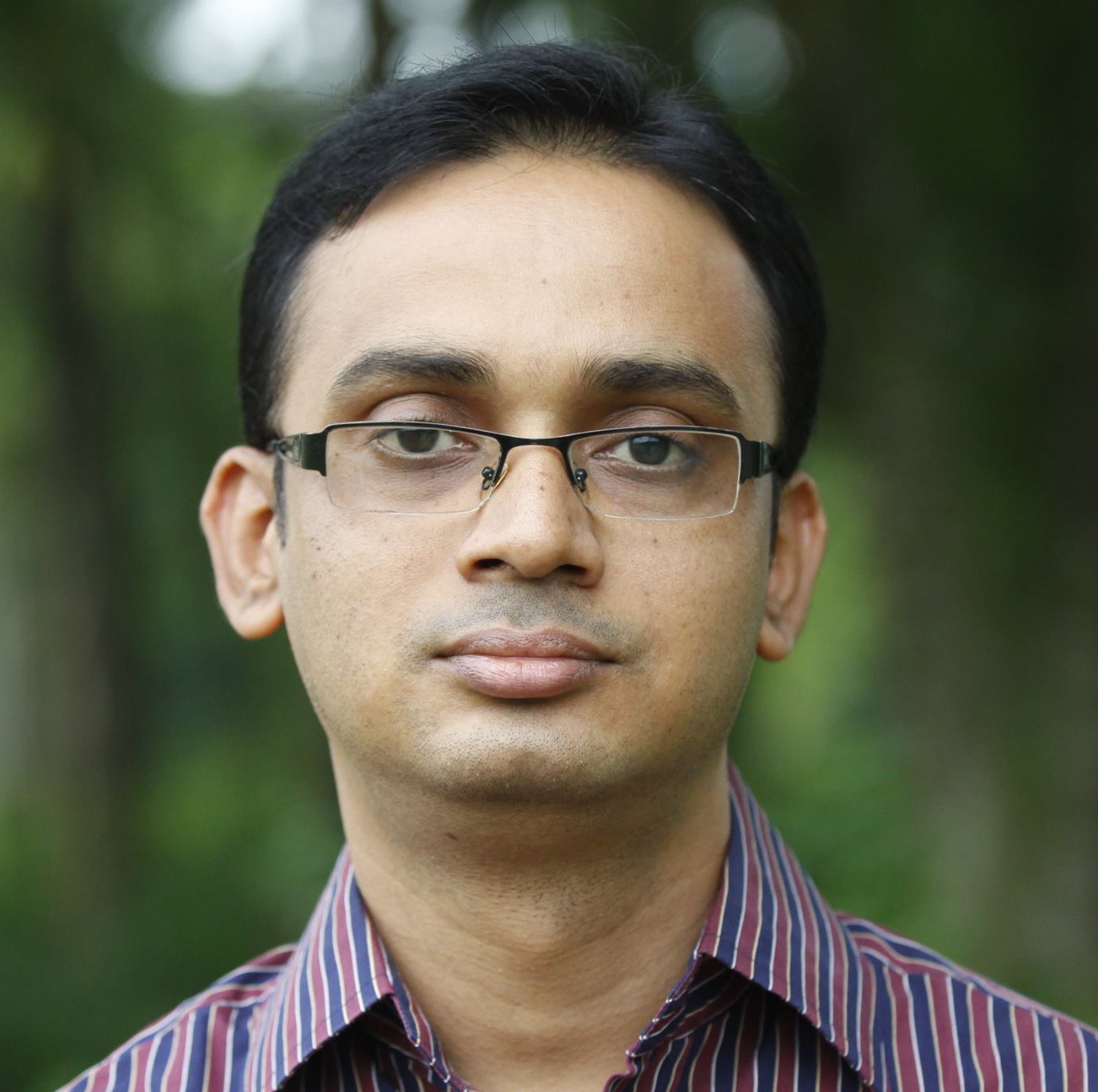

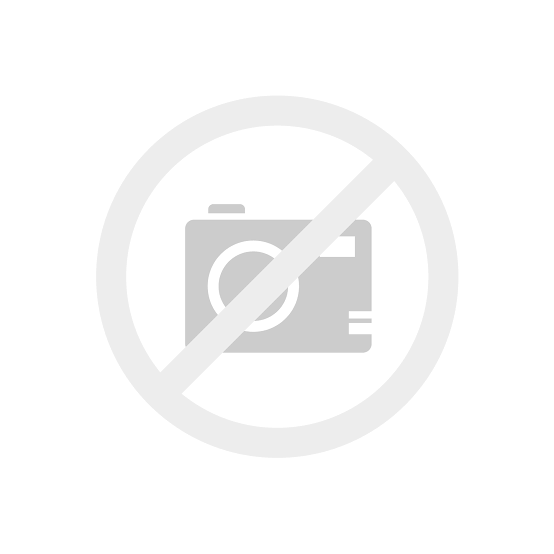
মন্তব্য করতে লগইন করুন অথবা নিবন্ধন করুন